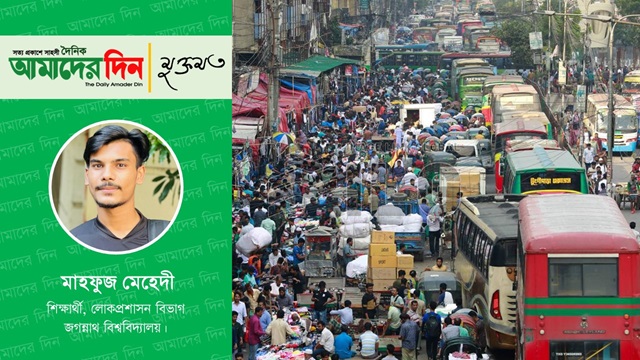টিআইবির গবেষণা
ই-জিপি চালু হলেও সরকারি কেনাকাটায় কমেনি দুর্নীতি

ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) চালু হওয়া সত্ত্বেও সরকারি কেনাকাটায় অনিয়ম ও দুর্নীতি কমেনি বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সংস্থাটি বলছে, ই-জিপি প্রবর্তনের ফলে সরকারি কেনাকাটা সহজ হয়েছে। একই সঙ্গে টেন্ডার বাক্স ছিনতাই, টেন্ডার সাবমিট করতে না দেওয়া, কার্যালয় ঘেরাও বন্ধ হয়েছে। কিন্তু দুর্নীতি কমার সঙ্গে ই-জিপির তেমন সম্পর্ক নেই। খোদ সরকারের বিভিন্ন কিন্তু দুর্নীতি কমার সঙ্গে ই-জিপির তেমন সম্পর্ক নেই। খোদ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারাই এ বিষয়ে একমত প্রকাশ করেছেন।
গতকাল বুধবার ‘সরকারি ক্রয়ে সুশাসন : বাংলাদেশে ই-জিপির কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ’ শীর্ষক এক গবেষণায় প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরেছে টিআইবি।
গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ই-জিপির অন্যতম প্রধান দুটি উদ্দেশ্য ছিল সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি হ্রাস করা ও কাজের মান বাড়ানো। তবে দুর্নীতি ও কাজের মানের ওপর ই-জিপির কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। রাজনৈতিক প্রভাবে ঠিকাদারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অধিকাংশ এলাকায় কারা টেন্ডার সাবমিট করবে সেটা রাজনৈতিক নেতা বিশেষ করে স্থানীয় সংসদ সদস্য ঠিক করে দেন। অনেক ক্ষেত্রে একটি বড় লাইসেন্সের অধীনে কাজ নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা তার কর্মীদের মাঝে বণ্টন করে দেন। দরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবহেলা, নিজেরা কাজ না করে কম্পিউটার অপারেটরদের মাধ্যমে মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি, নম্বর বাড়িয়ে-কমিয়ে আনুকূল্য দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অফিস কর্মকর্তারা ঠিকাদারদের রেট শিডিউল জানিয়ে দেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া অফিসের কম্পিউটার অপারেটরদের সাহায্যে নিয়মবহির্ভূত কাজ করানো হয়।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, লিমিটেড টেন্ডার মেথডে (এলটিএম) কার্যাদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের ঘুষ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ছাড়া কাজ তদারকি, অগ্রগতি প্রতিবেদনে ভুল তথ্য দেওয়া, কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর বিল তুলতে ঘুষ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। ওপেন টেন্ডার মেথডে (ওটিএম) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আগে থেকেই সিন্ডিকেট করা থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। কিছু কিছু এলাকায় ঠিকাদার, রাজনৈতিক নেতা ও সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগসাজশের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া অবৈধভাবে কাজ বিক্রি করা বা সাব-কন্ট্রাক্ট দেওয়া এবং একজনের সার্টিফিকেট ও লাইসেন্স ব্যবহার করে কাজ নেওয়া ও অন্যজনের কাজ করা হয়। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের চাঁদা দেওয়া বা দিতে বাধ্য হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার বাইরের ঠিকাদারদের কাজ করতে না দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে।
ই-জিপি পদ্ধতিতে তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ হওয়ার কারণে ভালো ও দক্ষ ঠিকাদারদের কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ফলে কাজ বাস্তবায়নে দুর্নীতি কমসহ কাজের মান ভালো হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের অধিকাংশের মতে, ই-জিপির সঙ্গে কাজের মানের সম্পর্ক নেই। তথ্যদাতাদের মতে, ই-জিপির কারণে কাজ ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কাজ বিক্রি করার কারণে তা নষ্ট হচ্ছে।
টিআইবির গবেষণা অনুযায়ী পল্লী বিদ্যুৎ (আরইবি) ৪৪ শতাংশ, পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) ৪৩ শতাংশ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ৪২ শতাংশ। প্রাপ্ত সার্বিক স্কোর অনুসারে সবগুলো প্রতিষ্ঠানের অবস্থানই ‘ভালো নয়’ গ্রেডে।
প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাপ্ত স্কোর থেকে দেখা যায়, সবগুলো প্রতিষ্ঠানই প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো ও প্রায় কাছাকাছি অবস্থানে (৬০-৭৫ শতাংশ), তবে সওজ ও আরইবির সক্ষমতা অন্য দুই প্রতিষ্ঠানের চেয়ে তুলনামূলক ভালো। ই-জিপি প্রক্রিয়া মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রায় সব প্রতিষ্ঠান কাছাকাছি অবস্থানে (৫৮-৬৪ শতাংশ) রয়েছে। অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখনো অনেক উন্নতির সুযোগ রয়েছে। ই-জিপি ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকারিতায় কোনো প্রতিষ্ঠানই কোনো স্কোর পায়নি বলে দেখা যায়। আবার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ক্ষেত্রে সব প্রতিষ্ঠানের স্কোর অনেক কম (১৯-৩০ শতাংশ)।
এ পরিস্থিতি উত্তরণে এক ডজন সুপারিশ করেছে টিআইবি। এর মধ্যে রয়েছে প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে করা, ই-জিপি পরিচালনায় কাজের চাপ ও জনবল কাঠামো অনুযায়ী ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে জনবল বাড়ানো, ই-জিপির সঙ্গে সম্পর্কিত সব অংশীজনকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনাসহ বেশ কিছু। ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে গবেষণা প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসির সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার নাহিদ শারমীন ও মো. শহিদুল ইসলাম।